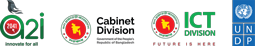-
About
Introduce to Upazila
History & Tradition
Geography & Economics
-
Upazila Parishad
উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান
স্থায়ী কমিটি
-
আ্ইন শৃংখলা বিষয়ে স্থায়ী কমিটি
-
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কমিটি
-
উপজেলা যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন কমিটি
-
জনস্বাস্থ্য,স্যানিটেশন,ও বিশুদ্ব পানি সরবরাহ কমিটি
-
উপজেলা পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় কমিটি
-
উপজেলা মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা কমিটি
-
উপজেলা পরিবেশ ও বন কমিটি
-
উপজেলা সংস্কৃতি কমিটি
-
উপজেলা মুক্তিযোদ্বা কমিটি
-
বাজার মূল্য পর্যবেক্ষন, মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রন বিষয়ক উপজেলা কমিটি
-
উপজেলা যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন স্থায়ী কমিটি
-
উপজেলা মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক স্থায়ী কমিটি
-
কৃষি বিষয়ক স্থায়ী কমিটি
-
উপজেলা সমাজকল্যান বিষয়ক স্থায়ী কমিটি
-
মহিলা ও শিশু বিষয়ক উন্নয়ন কমিটি
-
অর্থ,বাজেট,পরিকল্পনা ওস্থানীয় সম্পদ আহরণ কমিটি
-
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক কমিটি
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) অগ্রগতি প্রতিবেদন
-
আ্ইন শৃংখলা বিষয়ে স্থায়ী কমিটি
-
Administration
Upazilla Nirbahi Officer
About Organogram
Programs and Meeting
Services and Other
-
Goverment Offices
Land Affairs
Law and Order Affairs
Health Affairs
Agrculture and Food Related
Engineering and Communication
Human Resources Development Related
Education Related
- Project Management
-
Other Organizations
Educational Institutions
-
Matiranga Pourasova
পৌরসভা প্রশাসক
মাটিরাঙ্গা পৌরসভা সম্পর্কিত
-
About
Introduce to Upazila
History & Tradition
Geography & Economics
-
Upazila Parishad
উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান
Staffs
Acts & Regulations
উপজেলা পরিষদের মাসিক সাধারণ সভার কাযবিবরণী
স্থায়ী কমিটি
- আ্ইন শৃংখলা বিষয়ে স্থায়ী কমিটি
- উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কমিটি
- উপজেলা যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন কমিটি
- জনস্বাস্থ্য,স্যানিটেশন,ও বিশুদ্ব পানি সরবরাহ কমিটি
- উপজেলা পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় কমিটি
- উপজেলা মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা কমিটি
- উপজেলা পরিবেশ ও বন কমিটি
- উপজেলা সংস্কৃতি কমিটি
- উপজেলা মুক্তিযোদ্বা কমিটি
- বাজার মূল্য পর্যবেক্ষন, মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রন বিষয়ক উপজেলা কমিটি
- উপজেলা যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন স্থায়ী কমিটি
- উপজেলা মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক স্থায়ী কমিটি
- কৃষি বিষয়ক স্থায়ী কমিটি
- উপজেলা সমাজকল্যান বিষয়ক স্থায়ী কমিটি
- মহিলা ও শিশু বিষয়ক উন্নয়ন কমিটি
- অর্থ,বাজেট,পরিকল্পনা ওস্থানীয় সম্পদ আহরণ কমিটি
- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক কমিটি
উপজেলা পরিষদের সম্পদ বিবরণী
বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) অগ্রগতি প্রতিবেদন
উপজেলা পরিষদের বাজেট
মাটিরাঙ্গা উপজেলা পরিষদের পঞ্চবার্ষিকী উন্নয়ন পরিকল্পনা
-
Administration
ফটোগ্যালারী
Upazilla Nirbahi Officer
About Organogram
Programs and Meeting
Services and Other
-
Goverment Offices
Land Affairs
Law and Order Affairs
Health Affairs
Agrculture and Food Related
Engineering and Communication
Human Resources Development Related
Education Related
- Project Management
-
Other Organizations
Educational Institutions
-
Matiranga Pourasova
পৌরসভা প্রশাসক
মাটিরাঙ্গা পৌরসভা সম্পর্কিত
মাটিরাঙ্গা উপজেলায় ৩ টি ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী বসবাস করেঃ
পৃথিবীর সকল জাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, প্রত্যেক জাতি বা জনগোষ্ঠীর পৃথক বংশ পরিচয় ইতিহাস রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত ১৩ টি উপজাতির জীবন যাত্রা স্বতন্ত্র, বৈচিত্রময় কিন্তু সহজ সরল। এই নৃগোষ্ঠীসমূহের মধ্যে চাকমা, ত্রিপুরা ও মারমা পর্যায়ক্রমিক সংখ্যাগরিষ্ঠ।
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা তথা মাটিরাঙ্গা উপজেলা একটি জনবহুল অঞ্চল। এ অঞ্চলে প্রায় ৩ ধরণের জাতি বসবাস করে। তাদের নিজস্ব ভাষা ও ঐতিহ্য রয়েছে। সাধারণত বাঙ্গালীদের পহেলা বৈশাখকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন জাতির মধ্যে তাদের সংস্কৃতি ফুটে উঠে। যেমন : ত্রিপুরাদের বৈসু, মারমাদের সাংগ্রাই ও চাকমাদের বিজু এই তিনটি জাতি ভিন্ন ধর্মী নামকে মিলিয়ে বৈসাবি নামে আখ্যায়িত করেছে। যাতে করে এই অঞ্চলে মানুষদের মিলেমিশে তাদের সংস্কৃতি ফুটিয়ে তুলতে পারে।
(ক) চাকমাঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রথম ‘‘চাকমা’’ শব্দের অস্তিত্ত্ব এবং ষোড়শ শতাব্দীতে এ অঞ্চলে এ নামের একটি জনগোষ্ঠীর বসবাসের তথ্য পাওয়া যায়। এই চাকমা জাতিগোষ্ঠী শাব্দিক বা উচ্চারনগত দিক থেকে যাই হোক না কেন এরাই যে বর্তমানে চাকমা নামে পরিচিত জনগোষ্ঠী তাতে কোন সন্দেহ নেই। চাকমারা মূলতঃ বৌদ্ধ ধর্বাবলম্বী এবং বিজু তাদের প্রধান সামাজিক উৎসব । চাকমা সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী ‘‘জুম নৃত্য’’ দেশে-বিদেশে দারুণভাবে প্রশংসিত। তুলনামূলকভাবে চাকমারা অধিক শিক্ষিত। তবে চাকমা উপজাতীয় রমণীরা অত্যন্ত কর্মঠ ও পরিশ্রমী। চাকমাদের মধ্যে প্রচলিত কথ্য ভাষার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে স্পষ্টতঃ প্রমানিত হয় যে, তা বাংলা চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষারই অপভ্রংশ। চাকমারা চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষার অপভ্রংশের মতো উচ্চারণ রীতি ব্যবহার করলেও চাকমা ভাষার বর্ণমালা বর্মী আদলে তৈরি। ব্রিটিশ আমলে কর্মরত চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার মিঃ জিন বিসম ০৫ অক্টোবর ১৮৭৯ সালে রাজস্ব বোর্ডের নিকট লিখিত পত্রে উল্লেখ করেন, ‘‘চাকমাগণ’’ অর্ধ বাঙ্গালী। বস্তত্ব ইহাদের পোশাক পরিচ্ছেদ এবং ইহাদের ভাষাও বাংলা বিকৃত রূপ মাত্রা এতদ্ভিন্ন চাকমাদে উপাধি ভিন্ন নামগুলোও এমন বাঙ্গালী ভাবাপন্ন যে, তাহাদিগকে বাঙ্গালী হইতে পৃথক করা একরূপ অসম্ভব।
(খ) মারমাঃ পার্বত্য জেলাসমূহে মারমারা সংখ্যায় দ্বিতীয় হলেও খাগড়াছড়িতে এরা তৃতীয় সংখ্যাগরিষ্ট উপজাতি।
বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলাতেই মূলতঃ এদের বসবাস। মারমারা অত্যন্ত অতিথিপরায়ন। এ জনগোষ্ঠীর মেয়েরা অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। তারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এবং তাদের প্রধান সামাজিক উৎসব ‘‘সাংগ্রাই’’ । সাধারণতঃ মারমা বর্ষপঞ্জি ঘোষণাপত্র ‘‘সাংগ্রাইংজা’’ এর মাধ্যমে চান্দ্রমাস অনুসারে মারমারা তাদের প্রধান সামাজিক উৎসব ‘‘সাংগ্রাই’’ পালন করে থাকে। বহু পূর্বে মারমারা ‘‘মগ’’ নামেই পরিচিত ছিল। বর্তমানে তারা নিজেদের মারমা বলেই দাবী করে। মারমা শব্দটি মারমাজা বা ম্রাইমাচা নামক উপমহাদেশীয় প্রাচীন ব্রাহ্মী হস্তাক্ষর লিপি থেকে উদ্ভুত। স্বাধীনতা উত্তরা বাংলাদেশে সরকারিভাবে মারমা জনগোষ্টী স্বতন্ত্র উপজাতি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। মারমা ভাষায় নিজস্ব হরফও আছে। এ বর্ণমালা মারমাচা বা ম্রাইমাজাহ্ নামে পরিচিত। ১৩ টি স্বরবরর্ণ ও ৩৬ টি ব্যঞ্জণবর্ণ নিয়ে প্রণীত মারমা বর্ণমালা প্রাচীন ভারতের ব্রহ্মী ও খরেষ্ট্রী লিপি হতে উদ্ভুত। মারমারা বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী হলেও তারা অন্যান্য উপজাতীয়দের ন্যায় দেবতা ও অপদেবতায় বিশ্বাসী। তবে বৌদ্ধ ধর্মের অন্যান্য উৎসব পার্বণাদিও তারা পালন করে। মারমা জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী থালা নৃত্য, প্রদীপ নৃত্য, পরী নৃত্য অত্যন্ত আকষণীয়।
(গ) ত্রিপুরাঃ পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত আদিবাসীদের জাতি গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে ত্রিপুরারাই ইতিহাস সমৃদ্ধ জাতি। খ্রিষ্টাব্দ গণনার বহু পূর্ব হতেই এ অঞ্চলে ত্রিপুরাদের অস্তিত্ত্ব ছিল। মহাভারতে বর্ণিত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধেও ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী অংশ নিয়েছিল বলে জানা যায়। ৫৯০ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরা রাজা যুঝারুফা কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের পর স্মারক হিসেবে ত্রিপুরাব্দ প্রবর্তনের পর হতে ত্রিপুরাদরে লিখিত ইতিহাসের সুচনা ঘটে। সঠিক তথ্য জানা না গেলেও বহু আদিকাল থেকে এ অঞ্চলে ত্রিপুরাদের বসবাস ছিল। অধ্যাপক শাহেদ আলী তার বাংলা সাহিত্যে চট্টগ্রামের অবদান বইয়ে লিখেছেন- পাহাড়ী জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে ত্রিপুরারাই সবচেয়ে সংঘবদ্ধ ও শক্তিশালী। ত্রিপুরারা সনাতন ধর্মাবলম্বী। তাদের প্রধান উপজীবিকা কৃষি তথা জুম চাষ। তাদের প্রধান উৎসব বৈসাবী। উপজাতি প্রায় সকল রমনীরাই নিজেদের তৈরি তাতে বোনা কাপড় পড়ে। এদের পড়নের কাপড়কে রিনাই রিসাই বলে । রূপার তৈরি অলংকার ত্রিপুরা রমণীদের খুব প্রিয়। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী অত্যন্ত সমৃদ্ধা । ত্রিপুরাদের ঐতিহ্যবাহী গড়াইয়া ও বোতল নৃত্য অত্যন্ত প্রশংসনীয়। ত্রিপুরাদের মধ্যে রোয়াজা উপাধি ধারীরাই সামাজিক বিচার আচার করে থাকে।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS